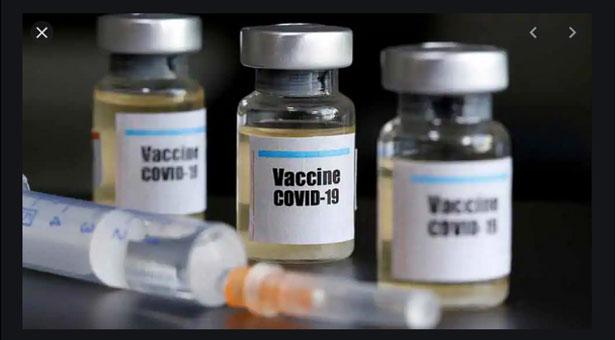নভেল করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিকিৎসার ওপরে ভরসা না করে প্রতিষেধক টিকা বা ভ্যাকসিনের ওপর জোর দেওয়ার বিষয়ে অধিকাংশ বিজ্ঞানী একমত। কারণ, ভাইরাসজনিত রোগের চিকিৎসার ওষুধের ইতিহাস এ পর্যন্ত খুব আশাব্যঞ্জক নয়। প্রযুক্তির আকাশচুম্বী উৎকর্ষ সত্ত্বেও অল্প কয়েকটি ভাইরাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ভাইরাসজিনত রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে খুবই নগণ্য। যেমন করোনাভাইরাস গ্রুপে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১২টা ভাইরাসের মধ্যে চিকিৎসার ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র একটির। সেটা হেপাটাইটিস-সি চিকিৎসার ওষুধ। আর কার্যকর টিকা আবিষ্কার করা গেছে ৬টির (ইয়োলো ফিভার, জাপানিজ এনকেফালাইটিস, হেপাটাইটিস ই, হেপাটাইটিস এ, পলিও, ও রুবেলা ভাইরাস)।
ফলে কোভিড-১৯ চিকিৎসার ওষুধ আবিষ্কারের চেয়ে আপাতত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের আশায়। এর মূল কারণ আমরা সবাই জানি, প্রতিকারের নয় প্রতিরোধই শ্রেয়। টিকাই হবে এই কভিড-১৯–এর প্রতিরোধ।
প্রথমেই বলে রাখি, আমি টিকা–বিশেষজ্ঞ নই। আমি ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অভিজ্ঞ এবং ওষুধ বা টিকা তৈরির পদ্ধতিতেই আমার অভিজ্ঞতা। টিকা আবিষ্কারের পর কী কী ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে টিকা বা ওষুধ ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়, সে বিষয়ে আলোকপাত করব। এই ধাপগুলো বুঝতে পারলেই মোটামুটি ধারণা করা যাবে, নভেল করোনাভাইরাসের টিকা পেতে আমাদের কত দিন অপেক্ষা করতে হতে পারে।
এখন পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে আনুমানিক ৯৫টি ভ্যাকসিনের এজেন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এই এজেন্টগুলোর কার্যকারিতা কেমন, এগুলোর ব্যবহার নিরাপদ কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়নি। এমনকি কোনো গিনিপিগ বা ওই জাতীয় প্রাণীর এগুলো প্রয়োগ করে গবেষণা করা হয়নি। একটি আদর্শ টিকা বা ওষুধের প্রধান দুই বৈশিষ্ট্যের এর নিরাপত্তা কার্যকারিতা। বিভিন্ন দেশে নভেল করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কবে নাগাদ একটি নিরাপদ ও কার্যকর টিকা পাওয়া যাবে, তা জানা যাচ্ছে না।
ভ্যাকসিন তৈরি ও বাজারজাত করার প্রক্রিয়া কীভাবে করা হয়ে থাকে এবং ভ্যাকসিন আবিষ্কার বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়েও কিছুটা আলোকপাত করব এই লেখায়।
ভ্যাকসিন প্রস্তুতের প্রক্রিয়া অনেকটা ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়ার মতোই। অর্থাৎ ওষুধ তৈরিতে গবেষণা, রেগুলেটরি এবং অনুমোদনের যে সব ধাপ পার হতে হয়, ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও মোটামুটি তা করতে হয়। প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, ভ্যাকসিনের ট্রায়েলে সুস্থ ভলান্টিয়ারের দেহে ভ্যাকসিন দিয়ে, ভলান্টিয়ারকে রোগীর বা রোগজীবাণুর সংস্পর্শে এনে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা দেখা হয়, অন্যদিকে ওষুধের ক্ষেত্রে রোগের সংস্পর্শে আসা রোগীর দেহে ট্রায়েলের ওষুধ প্রয়োগ করে ওষুধের কার্যকারিতা দেখা হয়। তাই ভ্যাকসিন তৈরির প্রক্রিয়াটি সুস্থ ভলান্টিয়ারের অংশগ্রহণের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়ার চেয়ে কিছুটা জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। ভ্যাকসিন প্রস্তুতের প্রক্রিয়ার প্রধান ধা গুলো হচ্ছে উদ্ভাবনী ধাপ, প্রি-ক্লিনিক্যাল বা অ্যানিমেল গবেষণা ধাপ, ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনা বা রেগুলেটরি রিভিউ, অনুমোদন, উৎপাদন, বাজারজাত, ও মান নিয়ন্ত্রণ। এর প্রতিটি ধাপ পার হওয়ার পরই আমরা একটি ওষুধ বা ভ্যাকসিন পেয়ে থাকি।
উদ্ভাবনী ধাপ
এই ধাপটা প্রাথমিক ধাপ। এটা মূলত গবেষণাগারে বা খাতা–কলমে হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একাডেমিক হাসপাতাল বা বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন প্রাইভেট গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রকম চিন্তাভাবনা পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণাগারের প্রথমে জীবাণু দ্বারা রোগ হওয়ার কারণ আবিষ্কার করে থাকেন। তবে তার আগে যে জীবাণুটির প্রতিষেধক আবিষ্কার করা হবে, সে জীবাণুর বিষয়ে বিজ্ঞানীর সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ জীবাণুটির চারিত্রিক গুণাগুণ, বাহ্যিক আকার, প্রকৃতি, জেনেটিক কনফিগারেশন, জেনেটিক পরিবর্তন, আবাহাওয়ার প্রভাব, আয়ুষ্কাল, সংক্রমণক্ষমতা, অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় জেনে নিতে হয়। নভেল করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান এখনো খুবই সীমিত, এর গতিবিধি সম্পর্কে আমরা এখনো অনেক কিছুই জানি না। উদ্ভাবনী ধাপের তথ্য–উপাত্ত বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার পর শুরু হয় তা নিয়ে গবেষকের বিশ্লেষণ এবং বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় ট্রান্সলেশন বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের কাজ। ট্রান্সলেশন বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের এজেন্টকে ল্যাব থেকে ব্যবহারের উপযোগী করা। ট্রান্সলেশন গবেষণার শুরুর ধাপটাকে বলা হয় প্রি-ক্লিনিক্যাল বা অ্যানিমেল ট্রায়াল বা প্রাণীর ওপর গবেষণা।
প্রি-ক্লিনিক্যাল বা অ্যানিমেল ট্রায়াল ধাপ
এটাকে সহজ ভাষায় বলা হয় গিনিপিগ গবেষণা। এই ধাপে উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন বা ওষুধের এজেন্টটি গিনিপিগ বা ওই জাতীয় প্রাণীর (মডেলের) ওপর প্রয়োগ করে সেটির কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ গবেষণাগারে উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন বা ওষুধের এজেন্টটি মানবদেহে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, কার্যকরী পরিমাণ বা ডোজের ওপর গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এমনকি ভ্যাকসিনটির প্রয়োগ, যেমন ইনজেকশন না ট্যাবলেট না ক্যাপসুল কোনটা বেশি কার্যকর হবে, তা–ও দেখা হয় এই পর্যায়ে। এই ধাপে এজেন্টটির বিষক্রিয়া ও কী পরিমাণ (ডোজ) ওষুধ বা ভ্যাকসিন রোগ চিকিৎসায় বা রোগপ্রতিরোধে কার্যকরী হতে পারে, তারও একটা ধারণা নেওয়া হয়। ধারণা নেওয়া হয় বলার কারণ অ্যানিমেল ট্রায়ালের কার্যকারিতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানবদেহে অনুরূপ হয় না।
ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ধাপ
প্রি-ক্লিনিক্যাল ধাপের উপাত্ত নিয়ে শুরু হয় এই ধাপ। এটি ব্যয়বহুল ও ক্ষেত্রবিশেষে সময়সাপেক্ষ। এই ধাপটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণও, কারণ এই ধাপ থেকেই শুরু হয় মানবদেহে পরীক্ষা ও গবেষণা। এই ধাপকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরে দেখা হয় ভ্যাকসিনের বিষক্রিয়া ও নিরাপত্তার দিকগুলো। এই ধাপটি শুরু করার জন্য প্রি-ক্লিনিক্যাল ধাপের উপাত্ত সংবলিত একটি প্রস্তাবনা ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বিজ্ঞানীদের দিয়ে পুনর্মূল্যায়ন করার পর মানবদেহে ভ্যাকসিনটি প্রয়োগের জন্য অনুমোদন দেয়। আপাতত সেটি শুধু গবেষণার কাজে মানবদেহে ব্যবহারের জন্য একটি আইএনডি (ইনভেস্টিগেশনাল নিউ ড্রাগ) নম্বর প্রদান করে। এই পর্যায়ে স্বল্প পরিসরের সুস্থ ও সবল ভলান্টিয়ার মানবদেহে ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করে দেখা হয় এর কোনো বিষক্রিয়া বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় কি না এবং মানবদেহে কী ধরনের বা কী পরিমাণের ইমিউনিটি বা প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয়। এ পর্যায়ে ভ্যাকসিনটির প্রাথমিক ডোজও নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ভ্যাকসিন ট্রায়েলের এই ধাপটি ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়েলের চেয়ে একটু দীর্ঘ। কারণ ভ্যাকসিন থেকে শরীরের নির্দিষ্ট রোগের প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হতে কিছুটা সময় নেয় এবং সে কারণেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতেও একটু বেশি সময় লাগে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ন্যূনতম ছয় মাস অপেক্ষা করা উচিত। আগের এক অভিজ্ঞতা বলে, সময় নিয়ে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না দেখার ফলে হামের কিল্ড ভ্যাকসিন থেকে এটিপিকাল মিজেলস নামে একটি নতুন রোগের সূত্রপাত হয়, ১৯৫৫ সালে পলিও ভ্যাকসিন থেকে প্যারালাইসিস হওয়া এবং রেসপিরেটরি সিন্সাইটাল ভাইরাস ভ্যাকসিন থেকে রোগটিতে রেজিস্ট্যান্স হওয়ার মতো জটিলতা দেখা দেয়। সুতরাং ভ্যাকসিন তৈরিতের তাড়াহুড়ো করলে বিপদের ঝুঁকি থাকে।
ভ্যাকসিন ট্রায়ালের তৃতীয় স্তরের জন্য আবারও একটি প্রস্তাবনা পরিপত্র ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বিজ্ঞানীদের দিয়ে পর্যালোচনা–পুর্নমূল্যায়নের পর মানবদেহে ভ্যাকসিন প্রয়োগের জন্য অনুমোদন দেয়। এই স্তরে ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ডোজ সুনির্দিষ্ট করার পাশাপাশি তার কার্যকারিতা দেখা হয়। সুস্থ সবল ব্যক্তিদের ট্রায়েলে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের সজ্ঞান অনুমতিসাপেক্ষে তাঁদের দেহে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে তাঁদের প্রাকৃতিকভাবে রোগটির সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হয়। দেখা হয় ভ্যাকসিনটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে রোগ থেকে প্রতিরক্ষা দিতে পারে কি না। তাদের ওপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ চালাতে হয়। সেই সঙ্গে ওই জনগোষ্ঠীর যারা ট্রায়েল ভ্যাকসিন নেয়নি, তাদের মধ্যেও রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা হয়। এই দুই ধরনের লোকের উপাত্ত থেকে ভ্যাকসিনটির কার্যকারিতা নিরূপণ করা হয়। এই স্তরে ভ্যাকসিন ট্রায়ালের জন্য প্রয়োজন ২০ থেকে ৩০ হাজার ভলান্টিয়ার। করোনাভাইরাস যেহেতু বৈশ্বিক মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এর ভ্যাকসিন পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আরও অনেক বেশিসংখ্যক ভল্টান্টিয়ারের প্রয়োজন হবে এবং তাতে বেশি সময় লাগবে। বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে ভলান্টিয়াররা যেহেতু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবেন না, সেহেতু ভ্যাসকিনের সঠিক পরীক্ষা হবে বেশ সময় সাপেক্ষ। কমপক্ষে তিন–চার বছর লেগে যাবে। তবে হিউম্যান চ্যালেঞ্জ স্টাডি নামে অন্য এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই স্তরের সময় কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব। ক্লিনিক্যাল ট্রায়েলের এই পর্যায়ে প্রায় ৬৯ শতাংশ ভাগ ভ্যাকসিনই বাদ পড়ে যায়।
হিউম্যান চ্যালেঞ্জ স্টাডি করা হয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়েলের তৃতীয় স্তরে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা দেখার জন্য। এই স্টাডিতে ট্রায়েলের ভ্যাকসিন মানবদেহে প্রয়োগের পর ট্রায়েলে অংশগ্রহণকারী ভলান্টিয়ারদের স্বেচ্ছাকৃত জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভলান্টিয়ার প্রয়োজন হয় মাত্র ৫০০ থেকে ১০০০ জন। কিন্তু ব্যাপারটা অমানবিক এবং অনৈতিক বিধায় প্রক্রিয়াটি প্রচলিত বা স্বাভাবিক নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এটা করা হয়। এ ধরনের স্টাডি আইআরবি (ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড) বা ইথিক্স কমিটির কাছ থেকে অনুমোদন পেতে হলে যথেষ্ট আত্মপক্ষ সমর্থনের উপাত্ত প্রয়োজন হয়।
যেহেতু বর্তমানে করোনাভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক ভ্যাকসিন নেই, সে ক্ষেত্রে তুলনামূলক পর্যালোচনা বাদেই কোনো ভ্যাকসিন ব্যবহার ও বাজারজাত করার অনুমোদন পেতে পারে। চতুর্থ ও শেষ ধাপে ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ভ্যাকসিনটি বাজারজাত করার পর তা ব্যবহারের বিশদ উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকবে এবং পর্যবেক্ষণের সমীক্ষা ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে থাকে।
এত কাঠখড় পোড়ানোর পর করোনাভাইরাসের যে ভ্যাকসিনটি আমরা পাব, সেটির কার্যকারিতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যাবে। ভ্যাকসিনটির পরীক্ষা হবে তরুণ–যুবক ভলান্টিয়ারদের ওপর। ষাটোর্ধ্ব বয়সীরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়েলের প্রোটোকলে বাদ পড়ে যাবেন। কারণ এই বয়সে অনেকেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকেন। সুতরাং তাঁদের জন্য ভ্যাকসিনটি কতটা কার্যকর হবে, তা বলা কঠিন হবে হবে। যেমন বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফ্লু ভ্যাকসিন কাজ করে না বললেই চলে। অথচ এই বয়সের জনগোষ্ঠীই করোনাতে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি, তাদের মৃত্যুর হারও বেশি। তাহলে করোনা ভ্যাকসিন মৃত্যুর হার কতখানি কমাবে, সেটা ঠিক বলা যাচ্ছে না।
আরেকটা প্রশ্ন, পৃথিবীর ৭৬০ কোটি মানুষের জন্য যে পরিমাণ ভ্যাকসিন প্রয়োজন হবে, তা উৎপাদন করতে কত সময় লাগবে। ভাইরাসটির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে মোট জনগোষ্ঠীর অন্তত ৭০ শতাংশকে ভ্যাকসিন দিতে হবে। এ থেকে হার্ড-ইমিউনিটি তৈরি হবে এবং আমরা করোনার বর্তমান রূপটির প্রকোপ থেকে হয়তো মুক্তি পাব। কিন্তু পরের বছরগুলোতে এই ভাইরাস যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে (স্ট্রেইন) ফিরে আসবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। পৃথিবীর ৭০ শতাংশ মানুষকে একটি করে ভ্যাকসিন দিতে হলে প্রয়োজন হবে প্রায় ৫৬০ কোটি ভ্যাকসিন। আমরা এখনো জানি না, ভ্যাকসিনটির ডোজ কী হবে বা এটি ফ্লু ভ্যাকসিনের মতো প্রতিবছরই নিতে হবে কি না। এই বিপুল পরিমাণ ভ্যাকসিন উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, পরিবহন নীতি (কোল্ড চেইন) মেনে বিতরণ, ও সর্বোপরি প্রয়োগ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। আমরা বাংলাদেশিরা কি এর ভাগ পাব? মার্কিন প্রেসিডেন্ট তো বলেই দিয়েছেন আমেরিকানদের অগ্রাধিকারের কথা। ভ্যাকসিনটি যদি আমেরিকায় আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হয়, তাহলে তো কথাই নেই। তারপর ভ্যাকসিনটির দাম নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কত হবে এর দাম, কে এর ব্যয় বহন করবে? এটা কি হবে শুধু উচ্চবিত্তদের জন্য? গরিব মানুষ পাবে না? আমাদের কোন সাহায্যকারী সংস্থার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবে?
ভ্যাকসিন তৈরির গুরু ডা. রবার্ট ভ্যান এক্সেন বলেছেন, নভেল করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা গেলে এটাই হবে আরএনএ ভাইরাসের জন্য প্রথম ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক। অনলাইন ভ্যাকসিন ট্র্যাকারে হিসাবমতে, আজ পর্যন্ত এই ভাইরাসের ৯৫টি ভ্যাকসিন উদ্ভাবনী ধাপ অতিক্রম করেছে। সেগুলোর মধ্যে আটটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের (মানবদেহে) বিভিন্ন স্তরে আছে, দুটো আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে। একটি আছে দ্বিতীয় স্তরে, দুটো আছে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে এবং তিনটি আছে প্রথম স্তরে। অবশিষ্ট সবগুলো আছে প্রি-ক্লিনিক্যাল ও প্রি-ক্লিনিক্যালের প্রস্তুতি ধাপে। এখানে বলে রাখা দরকার, কোনো কোনো ভ্যাকসিনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বিশেষ বিবেচনায় দুটো স্তর একই সঙ্গে শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়। করোনাভাইরাস ভ্যাকসিন ট্রায়ালের ক্ষেত্রে তা করা হচ্ছে। অবশ্য এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপাত্ত বা প্রমাণাদি দরকার হয়। আমেরিকায় প্রথম সারির একটি ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সময় বাঁচানোর জন্য ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা জানার আগেই তা উৎপাদনের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। যেন এটি নিরাপদ ও কার্যকর জানার সঙ্গে সঙ্গে বাজারজাত করতে পারে। ভ্যাকসিনের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যত ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কম সময় লেগেছে মামস ভ্যাকসিনে। তা–ও প্রায় চার বছর। আর আজ ৩০ বছর হয়ে গেছে এখনো এইডসের কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি। তবে আমি আশাবাদী। আমরা হয়তো স্বাভাবিক সময়সীমার অনেক আগেই পেয়ে যাব নভেল করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন। আবার কোলাহলে মুখরিত হবে গুলিস্তান, বাবুবাজার, সদরঘাট আর ফার্মগেট। এয়ারপোর্টে আপনজনের বিদায়ী ভিড়। দিন শেষে রাস্তায় রাস্তায় গার্মেন্টস থেকে ঘরে ফেরা মা-বোনের গাড়িতে ওঠার প্রতিযোগিতা। রাতের আঁধারে ঝলমল আলো জ্বেলে তির তির করে ছুটবে বরিশালের লঞ্চ।
ডা. আনওয়ারুল হক মিঞা, পিএইচডি, এমপিএইচ, এমবিবিএস
অগাস্টা ইউনিভার্সিটি, অগাস্টা, জর্জিয়া, ইউএসএ
(সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট প্রোগ্রাম)

 নিউজ ডেস্ক
নিউজ ডেস্ক